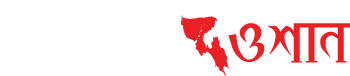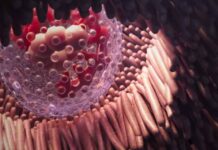এ্যাডঃ আবদুস ছালাম খান
মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মানবতাকে নাড়া দেয়া অনেক ঘটনা ঘটেছে। নিজের সন্তানকে এমনকি বৃদ্ধ মা-বাবাকে পথে ফেলে যাওয়ার মত মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছে। সে রকম একটি মর্মান্তিক ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তখন বৃহত্তর বরিশাল জেলা ও ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহাকুমার (বর্তমানে জেলা) অধিকাংশ শরণার্থীদের ভারতে যাবার রুট ছিল লোহাগড়ার উপর দিয়ে। বর্ষাকালে লোহাগড়া থানার বিভিন্ন স্থান থেকে নৌকা যোগে মাগুরা মহাকুমার গঙ্গারামপুর পর্যন্ত যাওয়া যেত। তাতে অন্ততঃ দীর্ঘ হাঁটা পথে কিছুটা হলেও বিশ্রাম হতো। শরণার্থীরা লোহাগড়া থেকে নৌকাযোগে গঙ্গারামপুর নেমে বরইচরা হয়ে পুলুম মধুখালির মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহ মহাকুমার কালিগঞ্জ রাস্তা পার হয়ে কোটচাদপুর ও চুয়াডাঙ্গা মহাকুমার বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতো। যদিও কালিগঞ্জের এই রাস্তা পার হওয়া ছিল এই রুটের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এই রাস্তা পার হতে শরণার্থীরা আখের জমির মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করতো। সুযোগ বুঝে দৌড়ে পার হয়ে যেত। রাজাকার বা টহলরত পাক আর্মিদের হাতে ধরা পড়লে মৃত্যু অথবা সর্বস্ব খোয়াতে হতো।
এভাবে লোহাগড়া থেকে একজন লোকের ভারতে পৌছাতে ৪/৫ দিন এবং বরিশাল থেকে ৭/৮ দিন লেগে যেত। বর্ষাকালে এই রুট ছিল আমাদের কুন্দশী গ্রামের তেমাথায় নবগঙ্গা নদীর ঘাট থেকে নৌকা যোগে মাগুরা জেলার গঙ্গারামপুর নেমে সেখান থেকে আবার পায়ে হাটা পথ। শরণার্থীদের এইভাবে পার করার জন্য পেশাদার পারের নৌকা ও তার মাঝিরা ছাড়াও গ্রামের জেলে ও পালেদের বড় বড় বাচাড়ি নৌকা নিয়ে অপেশাদার অনেকে এই কাজে নিয়োজিত হয়। এতে উভয়েই লাভবান হতো। এদিকে বৃষ্টি-বর্ষায় এবং শরণার্থীদের হাটার চাপে রাস্তায় কাদা-মাটির যে অবস্থা হয়েছিল তা বলে বোঝানো যাবে না।
কারণ সে সময়ে তো আর আজকের মত পাকা রাস্তা ছিল না। ফলে কাদা-মাটি মাড়িয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হাটা শরণার্থীরা ক্লান্ত হয়ে নৌকা পারের অপেক্ষায় কুন্দশী গ্রামে নদীর ঘাটে কিছু সময় বিশ্রাম নিত। রাতের বেলায় কোন নৌকা এখান থেকে ছেড়ে যেত না। রাত হলে এমন কি বেলা গড়িয়ে গেলে আর কোন নৌকা ছাড়তো না। কারণ রাতে যাওয়া অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাই বাধ্য হয়ে পরদিন সকাল পর্যন্ত ওই ঘাটে অপেক্ষা করতে হতো। কেউ কেউ আশপাশের বাড়িতে কোন রকমে রাত কাটানোর জন্য আশ্রয় নিত। অনেকে আবার গাছ তলায়ই রাত কাটিয়ে দিত। শরণার্থীদের এই সাময়িক বিশ্রামের সময় টুকুও নিরাপদ ছিল না। লোহাগড়া থানার খালেক পুলিশ মাঝে মাঝে রাজাকার ও সহযোগী পুলিশ নিয়ে শরণার্থীদের উপর হামলা করে তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ও মূল্যবান জিনিষপত্র কেড়ে নিত। ওই সময়ে পুলিশ বা রাজাকারদের তেমন প্রতিরোধের মুখে পড়তে হতো না। কারণ মুক্তিযোদ্ধারা তখনও ট্রেনিং নিয়ে দেশে আসে নাই। তবে নকশালরা মাঝে মাঝে ওদের কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করতো। নকশালদের সাথে মাঝে মাঝে গুলি বিনিময়ের ঘটনা দেখা গেছে। মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত বলতে গেলে নকশালরা দীর্ঘদিন এভাবে রাজাকার পুলিশদের মোকাবেলা করেছে।
গঙ্গারামপুর, পুলুম, মধুখালি এলাকাটি নকশালদের দখলে থাকায় এই পথে শরণার্থী যাওয়া নিরাপদ ছিল বলা যায়। আর তাই বরিশাল ফরিদপুরের হাজার হাজার শরণার্থী ভারতে যাবার জন্য এই রুট বেছে নেয়। এরকম একদিন বরিশালের একটি শরণার্থী পরিবার দীর্ঘ পথ পায়ে হেটে এসে ওই নদীর ঘাটে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তাদের সাথে থাকা একজন আশু সন্তান সম্ভবা প্রসূতি মহিলা দীর্ঘ পথ হেঁটে আসায় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হয়তো এত দীর্ঘ পথ হাটার চাপে তার প্রসব ব্যাথা শুরু হয়। পরিবারটি গ্রামবাসী কাউকে কিছু না বলে নদীর ঘাটে বিশ্রামের নামে অপেক্ষা করতে থাকে। সারারাত সেখানে থাকার পর ভোরে প্রসূতি মহিলা সেখানেই একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। প্রথম দিকে কেউ টের না পেলেও সন্তান প্রসবের পর স্থানীয়রা পরস্পর জানতে পেরে এগিয়ে যায়। তবে সে সময়ে ডাক্তার কবিরাজ তো আর সহজলভ্য ছিল না। গ্রামের মহিলারা তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে যে যতটুকু পারে সাহায্য করে। পরিবারটি কারো বাড়িতে না গিয়ে ওই ঘাটেই অবস্থান করতে থাকে। বিকালের দিকে খালেক পুলিশের দল ঝটিকা বেগে এসে ঘাটে থাকা শরণার্থীদের উপর হামলা চালায়। প্রাণভয়ে অন্যান্য শরণার্থীরা পালিয়ে যায়। কিন্তু প্রসূতি ওই মহিলা তার সদ্যজাত শিশু সন্তানটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে সেখানেই বসে থাকে। ক্রুদ্ধ খালেক পুলিশ বুটজুতা পায়ে লাথি মেরে প্রসূতি মহিলাকে ফেলে দেয়। মহিলা শিশু সন্তানসহ গড়িয়ে নদীর পানিতে পড়ে যায়।
এ দৃশ্য দেখে আমাদের গ্রামের কয়েকজন মহিলা দ্রুত এগিয়ে আসে। তারা প্রসূতি মহিলাকে উদ্ধার করে পরম মমতায় তার শিশু সন্তানটি ও ওই মহিলাকে যথাসম্ভব সেবা দেয়। আমার প্রতিবেশী রিজিয়া বেগম নামে একজন মহিলা শিশুটিকে কোলে নিয়ে সেবা করতে থাকেন। এ দৃশ্য দেখে ওই মহিলা বাচ্চাটিকে তার কাছে রেখে যেতে চান। মহিলার বুক ফাঁটা কান্না-কাটি দেখে রিজিয়া বেগমের ছেলেমেয়ে থাকায় তার মাতৃহৃদয় কথাটি অগ্রাহ্য করতে পারেনি। পরদিন মহিলা তার নাড়ী ছেড়া ধন শিশু সন্তানটিকে রিজিয়া বেগমের কাছে রেখে ভারতের উদ্দেশে চলে যায়। রিজিয়া বেগম শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে। শিশুটিকে পানি থেকে তুলে এনেছিলেন তাই তিনি তার নাম রেখেছিলেন ‘পানি’। রিজিয়া বেগম প্রায় ৬ মাস পানিকে মাতৃস্নেহে লালন পালন করলেও অবশেষে সে মারা যায়। একজন প্রসূতি মহিলার এ আত্মত্যাগ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা।
একটি জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ এই রাস্ট্রের জন্ম দিয়েছে। এ যুদ্ধে সকলের অবদান স্বীকৃত হওয়া উচিৎ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবদানের কথা তেমন বিচেনায় নেয়া হয় নাই। একইভাবে শরণার্থীদের অবদানও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নেয়া উচিৎ। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যারা আজ তালিকাভুক্ত হয়েছে তাদের অনেকেরই যুদ্ধ করতে হয়নি। তারা ট্রেনিং শেষ করে আসতে আসতে দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু যারা দেশে থেকে পাক বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর, পিস কমিটির নির্মম নির্যাতন অত্যাচারের স্বীকার হয়েছে তাদের মুক্তিযুদ্ধের কোন তালিকায় তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের মুক্তিযোদ্ধার ভাতা কে দেবে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধার প্রচলিত সজ্ঞা অনুসারে সাধারণ মানুষের অবদানের কোন স্বীকৃতি নেই বললেই চলে। কেউ কেউ শরণার্থীদের কেবলমাত্র পালিয়ে যাওয়া একদল জনগোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। তাদের মতে শরণার্থীরা পালিয়ে ভারতে গিয়ে নিরাপদে ছিল এবং সেখানে রেশন তুলে খেয়ে আরামেই ছিল।
মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের ভিতরে থেকে পাক বাহিনীর অত্যাচর নির্যাতন সহ্য করে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে , খাবার দিয়ে, এক গ্লাস পানি খাইয়ে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে সেই সাধারণ মানুষ ও শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া মানুষের আর্তনাদের কথা রয়ে গেছে শুধু সিনেমা, কবিতা ও গানে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যিনি পাক বাহিনী বা রাজাকারের ভয়ে দৌড়ে পালাননি, যাদের ঘর পোড়েনি, যাদের ভিটে-মাটি দখল হয়নি, পাক আর্মি বা রাজাকারের দ্বারা যার কোন নিকটাত্মীয়া ধর্ষিতা হয়নি, যারা তাদের নৃশংসতা দেখেনি, যারা ভিটে মাটি ছেড়ে শরণার্থী হয়ে ভারতে যাননি এমনকি শরণার্থীদের ৫/৭ দিন পায়ে হাটার দৃশ্য দেখেননি , যিনি শরণার্থী শিবিরে থাকেন নি তিনি বা তারা বুঝবেন না কত দাম দিয়ে এই স্বাধীনতা কিনতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর-রাজাকাররা সারা দেশে যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও লুঠপাট অগ্নিসংযোগ চালিয়েছিল তা মানব ইতিহাসের এক নির্মম অধ্যায়। তখন এ দেশের মানুষ প্রাণে বাঁচতে ভিটে মাটির মায়া ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের অধিকাংশেরই ঠাই হয়েছিল ভারতের শরণার্থী শিবিরে। তবে শরণার্থী শিবির পর্যন্ত পৌছাতে তাদের যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল তা অবর্ণনীয়। আবার শরণার্থী শিবিরের দুরাবস্থাও ছিল বর্ণনাতীত।
অর্থ্যাৎ শরণার্থী শিবিরেও তারা মানবেতর জীবন-যাপন করেছে। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পে অক্সফাম-ইউকে এর ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী জুলিয়ান ফ্রান্সিস নামক একজন ব্রিটিশ ত্রাণ কর্মকর্তা লিখেছেন, ‘নয়’শ শরণার্থী শিবিরে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি কিভাবে আশ্রয় নিয়েছিল তা ভাবতে আমার অবাক লাগে’। (তথ্য সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো)
তবে এটা সত্য যে শরণার্থীদের দুরাবস্থা দেখেই সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের দেখেই পাকসেনাদের বর্বরতার খবর বিশ্ববাসী জেনেছিল এবং বিশ্বব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ লক্ষ-কোটি শরণার্থীর দুঃখ বেদনার ইতিহাস আড়ালেই রয়ে গেছে। যদিও শরণার্থী হিসাবে যারা ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের অধিকাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ের। পাকিস্তানী শাসকরা ও তাদের সেনাবাহিনী বাঙ্গালী নিধনে প্রথমে হিন্দু জনগোষ্ঠিকেই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সকলেই তাদের নির্মমতার শিকার হয়েছিল। হিন্দু জনগোষ্ঠি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল বলেই হয়তো ভারত সরকার বেশি সোচ্চার হয়েছিল। আর তার সুফল আমরা সকলেই পেয়েছি। লেখা চলবে। (লেখক সিনিয়র আইনজীবী ও সাংবাদিক এবং সভাপতি লোহাগড়া প্রেসক্লাব)